
চারুবাক: অনিকেত চট্টোপাধ্যায়ের এই ছবি ‘শঙ্কর মুদি’ তৈরি হয় বছর পাঁচেক আগে। আর ছবির সময়কাল সম্ভবত আরও বছর দশ পিছিয়ে। কখন বিশ্বায়ন, ভুবনায়ন, আন্তর্জাতিক বাজার ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রতি মোহগ্রস্ত আমরা। সবার জন্য ‘বাজার’ খুলে দেওয়া মানেই ব্যবসায়ীদের যেমন অবাধ স্বাধীনতা, তেমনই কর্পোরেট এবং মাল্টি-ন্যাশনাল সংস্থাগুলির যে রমরমা সেটা বুঝেই আনন্দে ষোলোআনা হয়েছিলাম আমরা। পৃথিবীর সমস্ত নামী ব্র্যান্ডের পোশাক-আশাক, সুগন্ধীর মতো উপভোগ্য বস্তুর জন্য আর দুবাই, সিঙ্গাপুর, লন্ডন, প্যারিসে মার্কেটিং-এর জন্য ‘বেড়াতে’ যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। সবই মিলবে হাতের তেলোয়। বাড়ির পাশের কিংবা শহরের শপিং মলে। সেই ঝাঁ চকচকামির পাশেই যে গত দু’তিনশো বছরের ঐতিহ্য বহন করা শঙ্কর মুদিদের দোকান, পরান নাপিতের সেলুন, মঙ্গলা মাসির ব্লাউজের দোকান, মিনুদের হাতে বানানো কাগজের ঠোঙা, কিংবা প্রহ্লাদের চায়ের সকাল-বিকেলের আন্তরিক-ঘরোয়া আড্ডাগুলো যে চিরতরে হারিয়ে যাবে সেটা তথাকথিত বড়লোক উন্নয়নের চশমা দিয়ে দেখতে পাইনি আমরা। এখন সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।
চিত্রনাট্যকার-পরিচালক অনিকেত চট্টোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন চক্রের এমন ক্রিয়াকর্মকেই একটি ক্যাপসুল আকারে ধরার ও দেখানোর চেষ্টা করেছেন ‘শঙ্কর মুদি’ ছবিতে। বিশ্বায়নের মুখোশ আসলে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট জগৎ ও ব্যবসায়ীমহলের বিশ্ববাজার কুক্ষিগত করার এমন ঘৃণ্য পরিকল্পনার স্বপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি অবশ্যই রয়েছে। অনিকেত কলকাতার শহরতলির একটি ছোট্ট পরিসরে ‘বিশ্বায়ন’-এর কুফলটাকেই ধরেছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বাবাবিক কারণেই সমালোচনা ও প্রশংসা দুই-ই পাবে।
[ সুজয়ের হাতের ছোঁয়ায় কেমন হল ‘বদলা’? ]
কিন্তু অ্যাড এ সিনেমা বা ভেহিকল অফ প্রোটেস্ট হিসেবে ‘শঙ্কর মুদি’ কতটুকু উতরোলো, সেটাই বিবেচনার। সিনেমা তৈরির সাধারণ ব্যাপারটাই হল ‘ইলিউশন অফ রিয়ালিটি’। সাধারণ ক্যামেরার সামনে পরিবেশ বানিয়ে চরিত্র ও ঘটনা দিয়ে বাস্তবের ইলিউশন তৈরি করা। তৈরির কৃৎকৌশলে দর্শক কিন্তু সেটাকেই ‘বাস্তব’ মনে করবেন। এই ‘শঙ্কর মুদি’ কি সেটা করতে পারল? জিজ্ঞাসা সেখানেই। শঙ্কর মুদির মতো হৃদয়বান মানুষ তাঁর স্ত্রীর মতো বাস্তব গিন্নি, সেলুনের মালিক, পাড়ার মস্তান, পাগলা বহুরূপী, পাড়ার এইসব দোকান এলাকা ভেঙে স্বপ্নের ‘মল’ তৈরির ব্যবসায়ী সকলেই জীবন্ত চরিত্র। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কের মিল-অমিল, টানা-পোড়েন, প্রেম-প্রীতি, সম্পর্কের অভিঘাতগুলো অধিকাংশই লেগেছে সাজানো, কৃত্রিম। ফলে ছবির উদ্দেশ্যটাই ব্যহত হয়। দর্শক কখনই একাত্ম হতে পারেন না। এপিসোডিক্যালি ঘটনাগুলো অবাস্তব নয়। কিন্তু পারস্পরিক মেলবন্ধনে যোগাযোগের অভাব চিত্রনাট্যে।
কবীর সুমনের সুরে একটি গান মন্দ লাগেনি। সব চাইতে ভাল লেগেছে শিল্পীদের অনাবীল অভিনয়। নাম চরিত্রে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পাঁচ বছর আগেই প্রমাণ করেছিলেন তিনি কেমন এবং কোন রেঞ্জের অভিনেতা। তাঁর বিহেভিয়ারটাই বুঝিয়ে দেয় তিনি আমাদের চেনা পাড়ার চেনা মুদির দোকানের মালিক কাম কর্মচারী। ঘরোয়া স্ত্রীর চরিত্রে শ্রীলা মজুমদার তুলনাহীন। কাঞ্চন মল্লিক, রুদ্রনীল ঘোষ, অঙ্কিতা চক্রবর্তী, এমনকী ছোট্ট চরিত্রে যিশু সেনগুপ্তও তাঁদের ঝলক দেখিয়েছেন। কিন্তু চিত্রনাট্যের দুর্বলতায় এবং একজিকিউশনের কৌশলী অনুপস্থিতিতে অনিকেত একটি চলমান সমস্যাকে হাতের মুঠোয় ধরেও দর্শকের মনের কাছে পৌঁছতে পারলেন না। যদিও ইতিমধ্যেই বিশ্বায়নের কাঁপানো বেলুন চোপসাতে শুরু করেছে।
[ হিংসুটে বা মুখরা নয়, এক অন্য শাশুড়ি-বউয়ের গল্প দেখাল ‘মুখার্জিদার বউ’ ]
খবরের টাটকা আপডেট পেতে ডাউনলোড করুন সংবাদ প্রতিদিন অ্যাপ

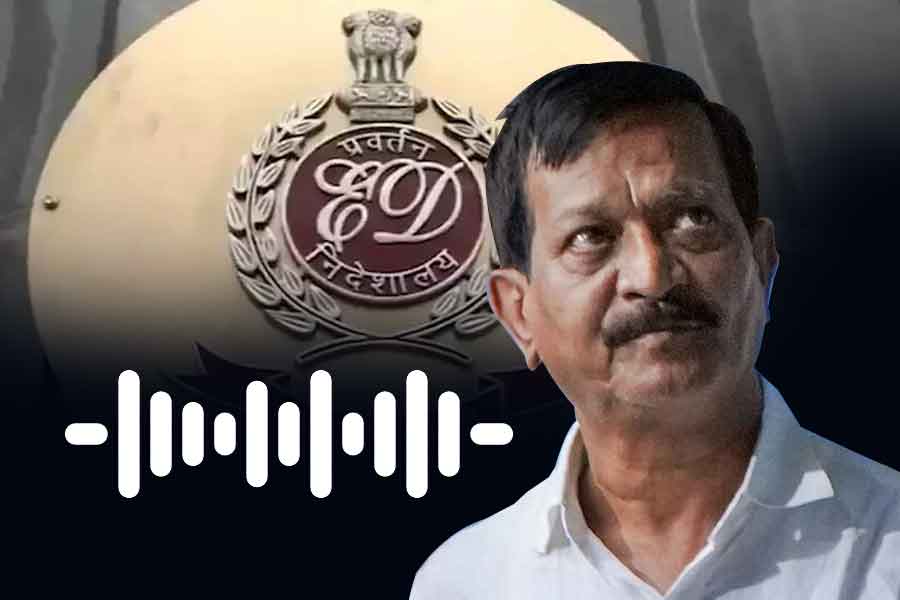
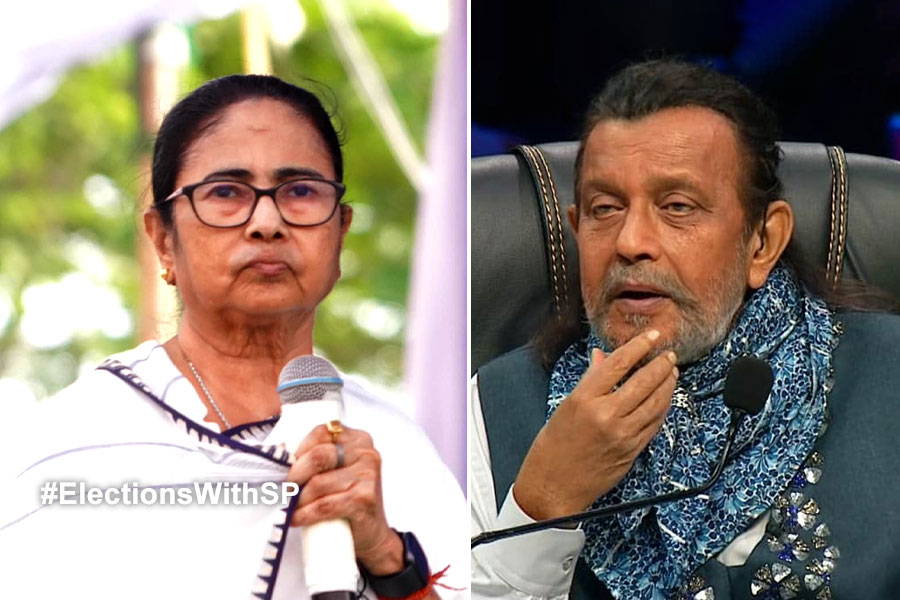


Copyright © 2024 Pratidin Prakashani Pvt. Ltd. All rights reserved.